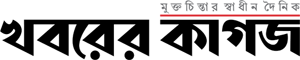একাত্তরের যুদ্ধ মুক্তির ছিল, নাকি স্বাধীনতার? উভয়েরই। ৭ মার্চের সেই বিখ্যাত জনসভায় শেখ মুজিবুর রহমান দুয়ের কথাই বলেছিলেন; ‘এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।’ তখন এবং যুদ্ধের পরও এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্য করা হয়নি। কিন্তু পার্থক্য নিশ্চয়ই ছিল। নইলে পরে জিয়াউর রহমানের সময়ে সংবিধানে যে পরিবর্তন আনা হয়েছে তাতে ‘মুক্তি’ সরিয়ে নিয়ে সে জায়গায় ‘স্বাধীনতা’ বসানো হলো কেন, কেন প্রয়োজন পড়ল এই সংশোধনের? স্মরণ করা যাক, আমাদের আদি সংবিধানের প্রস্তাবনার শুরুতে, এক নম্বর অনুচ্ছেদেই বলা হয়েছিল, ‘আমরা বাংলাদেশের জনগণ ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসের ২৬ তারিখে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া জাতীয় মুক্তির জন্য ঐতিহাসিক সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করিয়াছি।’ ১৯৭৮-এ জারি করা এক ফরমানের বলে সংবিধানে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনা হয়েছে। প্রস্তাবনার ওপরে লেখা হয়েছে, ‘বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম’ এবং প্রথম অনুচ্ছেদের যেখানে ছিল ‘জাতীয় মুক্তির জন্য ঐতিহাসিক সংগ্রাম’-এর কথা, সেখানে তো বদল করে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে ‘জাতীয় স্বাধীনতার জন্য ঐতিহাসিক যুদ্ধ।’ শুধু তাই নয়, এর পরে দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে যেখানে অঙ্গীকারের কথা আছে সেখানেও ‘জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম’ কেটে বসানো হয়েছে ‘জাতীয় স্বাধীনতার যুদ্ধ’।
সেই সঙ্গে যোগ করা হয়েছে সর্বশক্তিমান আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থার কথা এবং বাদ দেওয়া হয়েছে ধর্মনিরপেক্ষতা। আদি সংবিধানে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার ছিল এবং তার স্থান ছিল জাতীয়তাবাদের পরই। অর্থাৎ প্রথম অঙ্গীকার জাতীয়তাবাদের, দ্বিতীয় অঙ্গীকার সমাজতন্ত্রের। সংশোধনীতে সমাজতন্ত্র বাদ দেওয়া হয়নি সত্য, কিন্তু তাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে সর্বশেষে এবং সমাজতন্ত্র বলতে কী বোঝানো হচ্ছে তাও বলে দেওয়া হয়েছে। সমাজতন্ত্র অর্থ ‘অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচার।’ আদিতে নাগরিকদের জাতীয়তাবাদ ছিল বাঙালি, সংশোধনের ফলে তা দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশি। সংবিধানের দুটি পাঠ ছিল, একটি বাংলা, অপরটি ইংরেজি; বলা হয়েছিল অর্থের ব্যাপারে দুই পাঠের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে বাংলা পাঠই গ্রাহ্য হবে। ১৯৭৮-এর সংশোধনীতে বলা হয়েছে বিরোধের ক্ষেত্রে ইংরেজি পাঠই প্রাধান্য পাবে। সংশোধনগুলো মোটেই পরস্পরবিচ্ছিন্ন নয়; তারা একটি অভিন্ন চিন্তাধারার প্রতিফলন বটে। ওই চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে আছে একেবারে সূচনাতেই, প্রস্তাবনার সংশোধনীতেই যেখানে ‘জাতীয় মুক্তির জন্য ঐতিহাসিক সংগ্রাম’কে রূপান্তরিত করা হয়েছে ‘জাতীয় স্বাধীনতার জন্য ঐতিহাসিক যুদ্ধে’। ব্যাপারটা যত নিরীহ মনে হয় তত নিরীহ নয়। যুদ্ধ একাত্তরের ব্যাপার বটে, কিন্তু সংগ্রামের ইতিহাস অনেক দীর্ঘ, সংগ্রাম একাত্তরে শুরু হয়নি, শেষও হয়নি। ১৯৭৮-এ যারা রাষ্ট্রক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত তারা যুদ্ধটাকেই দেখতে চেয়েছেন। সংগ্রামকে উপেক্ষা করে। যুদ্ধে তারা ছিলেন, সংগ্রামে ছিলেন না। আর মুক্তি ও স্বাধীনতা যে এক নয় তাও তারা খেয়াল করেছেন। মুক্তি অনেক ব্যাপক ও গভীর ব্যাপার। স্বাধীনতা বলতে রাজনৈতিক স্বাধীনতা বোঝানো সম্ভব, কিন্তু মুক্তি বলতে বোঝাবে সার্বিক মুক্তি। হ্যাঁ, স্বাধীনতার জন্য লড়াই হয়েছে একাত্তরে। অবশ্যই। পাকিস্তানি রাষ্ট্রের অধীনতা থেকে বের হয়ে এসে আমরা একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছি। কিন্তু সেটা একমাত্র লক্ষ্য ছিল না। অথবা বলা যায়, মূল লক্ষ্য ছিল অনেক বিস্তৃত। সেটা ছিল জনগণের মুক্তি। যে জন্য রাষ্ট্রীয় মূলনীতিতে জাতীয়তাবাদের পাশাপাশি সমাজতন্ত্রের উল্লেখ করতে হয়েছে, বলতে হয়েছে ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্রের কথা। অঙ্গীকার করতে হয়েছে এ চারটি মূলনীতি প্রতিষ্ঠার। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা প্রয়োজন ছিল ওই সর্বাত্মক লক্ষ্যে পৌঁছার জন্যই। স্বাধীনতা প্রথম পদক্ষেপ, মুক্তি চূড়ান্ত লক্ষ্য। সংগ্রাম ছিল মুক্তির।
মুক্তির জন্য সংগ্রামটা দীর্ঘকালের। এ লড়াইয়ে নানা মানুষ এসেছে, সংগঠন এসে যোগ দিয়েছে। সবার ভূমিকা সমান নয়। নানা মাত্রার ও মাপের। কিন্তু সব স্রোত মিলেই বৃহৎ ধারাটি তৈরি। হঠাৎ করে অভ্যুত্থান ঘটেনি। ভুঁইফোড় নয়। একাত্তরে শুরু নয়, শেষও নয়। মুক্তির সংগ্রাম এখনো চলছে এবং চলবে।
মুক্তিযুদ্ধ ছিল ওই জনগণেরই যুদ্ধ। তারাই লড়েছে। কোনো একটি রণাঙ্গনে নয়, সর্বত্র, সব রণাঙ্গনে; কেবল দেশে নয়, বিদেশেও। বলা হয়েছে, যোদ্ধাদের শতকরা ৮০ জন ছিল কৃষক। এ কোনো অতিরঞ্জন নয়। গ্রামে-গ্রামে, প্রান্তে-প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল ওই যুদ্ধ। পাকিস্তানি শাসকদের মধ্যে কুটিল যারা তারা আশা করেছিল সংঘর্ষ সীমাবদ্ধ থাকবে। বেছে বেছে হত্যা করা হবে। কট্টর আওয়ামীপন্থি, ছাত্র, পুলিশ, বিদ্রোহী সেনা- এদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখবে হত্যাকাণ্ড। কিন্তু পারেনি, নৃশংস সৈন্যদের লেলিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তারা বাছবিচার করেনি। আর জনগণও বসে থাকেনি। আক্রমণকে তারা কোনো বিশেষ গোষ্ঠীর ওপর আঘাত হিসেবে দেখেনি, দেখেছে তাদের নিজেদের ওপর আক্রমণ হিসেবে। সেভাবেই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। অংশ নিয়েছে যুদ্ধে। ভাষা আন্দোলনের সময়েও এ রকমটাই ঘটেছিল। আন্দোলন শুরু হয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায়, প্রথম দিকে সীমাবদ্ধ ছিল সেখানেই। কিন্তু বায়ান্নর একুশে ফেব্রুয়ারিতে যখন ছাত্রহত্যা ঘটল, তখন আন্দোলন ছড়িয়ে গেল সারা দেশে। ছাত্রহত্যাকে দেশবাসী নিজেদের ওপর আক্রমণ হিসেবেই দেখেছে, অন্য কোনোভাবে নয়। এর আগে পুলিশ ধর্মঘট হয়েছিল। হত্যা করা হয়েছিল বেশ কয়েকজন বাঙালি পুলিশকে, কিন্তু সে ঘটনা বায়ান্নর ঘটনার মতো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারেনি। এর কারণ হচ্ছে এই যে, পুলিশের সঙ্গে জনগণের বিচ্ছিন্নতা ছিল, ছাত্রের সঙ্গে ছিল না। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন বেগবান ও সফল হয়েছে জনগণের অংশগ্রহণের ফলে। অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা স্বীকৃতি পেয়েছিল জনগণের কারণে।
জনগণই পাকিস্তান এনেছিল ভোট দিয়ে ১৯৪৬-এ। তারাই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে চলে গেছে বায়ান্নতে। ১৯৫৪-এর নির্বাচনে স্পষ্ট রায় দিয়েছে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে। সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে ঊনসত্তরের অভ্যুত্থান জনগণেরই অভ্যুত্থান বটে। মূল লক্ষ্য একটাই, মুক্তি। মুক্তির এ লক্ষ্যকে সামনে রেখেই একাত্তরের যুদ্ধ, যে যুদ্ধে পরাভূত হয়েছিল দুর্ধর্ষ বলে কথিত পাকিস্তানি সেনাবাহিনী। যুদ্ধের পেছনে যে চেতনা সেটা মুক্তির, যে মুক্তির সংজ্ঞা পাওয়া গেছে রাষ্ট্রীয় মূলনীতিতে। মূলনীতিগুলো যুদ্ধে জনগণের অংশগ্রহণ থেকেই বের হয়ে এসেছে, স্বাভাবিকভাবে। নইলে কারও সাধ্য ছিল না তাদের সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করে; যেমন যুদ্ধের সময়ে ও তার অব্যবহিত পরে কারও সাধ্য ছিল না তাদের অস্বীকৃতি জানায়। শাসনক্ষমতা যখন জনগণের কাছ থেকে দূরে সরে গেল, তখনই সম্ভব হয়েছে মূলনীতির সংশোধন। মুক্তির জায়গায় এসেছে স্বাধীনতা।
মুক্তির-যুদ্ধ ছিল একটা স্বতঃস্ফূর্ত সংগ্রাম। স্বতঃস্ফূর্ততার বহু গুণ ও সীমাবদ্ধতা তার মধ্যে পাওয়া যাবে। প্রধান গুণ হচ্ছে যুদ্ধের শক্তি ও বেগ; প্রধান দুর্বলতা তার সংগঠিত রূপ। যুদ্ধটা সংগঠিত, পরিকল্পিতভাবে শুরু হয়নি, চলেওনি। বিপরীতে পাকিস্তানিরা ছিল অত্যন্ত সুসংগঠিত ও সুসজ্জিত। তাদের ছিল বিদেশি শক্তির সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ। যুদ্ধ যখন শুরু হয় তখন মিত্র বলতে বাঙালির প্রায় কেউই ছিল না। ভারত যে যুক্ত হয়েছে তা আগের কোনো যোগাযোগের কারণে নয়, ঘটনা পরম্পরায়। একে সে প্রতিবেশী, তার ওপর ছিল শরণার্থীর বোঝা।
এমনকি যারা ছিল নেতৃত্বে সেই আওয়ামী লীগও এ কথা বলেনি যে, যুদ্ধ তারা শুরু করেছে। বলেছে যুদ্ধ তাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া আওয়ামী লীগ যে ঐক্যবদ্ধ ছিল তাও নয়। সেখানে যেমন তাজউদ্দীন আহমদ ছিলেন, তেমনি ছিলেন খন্দকার মোশতাক আহমদ। তাজউদ্দীন আপসে বিশ্বাসী ছিলেন না, খন্দকার মোশতাক সব সময়ই আপসের পথ খুঁজছিলেন। কিন্তু তাজউদ্দীনের আশপাশে যারা ছিলেন তারাও সবাই যে তার সঙ্গে ছিলেন; তা নয়। বিরোধ ছিল, যে জন্য মুক্তিবাহিনীর সমান্তরালে মুজিব বাহিনী গঠিত হয়েছিল। খন্দকার মোশতাকরা যে শক্তিহীন ছিলেন না তা বোঝা গেছে ১৯৭৫-এর নির্মম হত্যাকাণ্ডে। এও তাৎপর্যহীন নয় যে, তার আগেই মন্ত্রিসভা থেকে তাজউদ্দীন বাদ পড়ে গেছেন, মোশতাক বাদ পড়েননি। যুদ্ধের সময়ে জাতীয় সরকার গঠনের দাবি উঠেছিল। সেটা গৃহীত হয়নি। হওয়ার কথাও নয়। তবে ছাড় হিসেবে একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হয়েছিল, কিন্তু সেই পরিষদের একটিরও বেশি বৈঠক হয়নি। জাতীয় সরকার গঠনের দাবি স্বাধীনতার পরও তোলা হয়েছিল। গ্রহণযোগ্যতা পায়নি।
স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে শত্রু কে ছিল? শত্রু ছিল তারাই যারা জাতীয় মুক্তির বিপক্ষে ছিল। অর্থাৎ আল-বদর, রাজাকারসহ সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদের সমর্থকরা। দক্ষিণপন্থিরা। শত্রু ছিল তারা যারা মুক্তিযুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে মনে করেছে এবং নতুন রাষ্ট্রকে সামনের দিকে এগোতে না দিয়ে পেছন দিকে ঠেলে দিতে চেয়েছে, বড় পাকিস্তান ভেঙে ছোট পাকিস্তান গড়বে ভেবেছে। ১৯৭৮-এর সাংবিধানিক সংশোধনগুলো দক্ষিণপন্থিদেরই কাজ। এরশাদের সময়ে পুঁজিবাদের পথকে আরও প্রশস্ত করা হয়েছে। রাষ্ট্রীয় ধর্ম প্রবর্তন পশ্চাৎগমনেচ্ছুদের আরেকটি বিজয় চিহ্ন। দুঃখজনক হলেও সত্য মুক্তিযুদ্ধের চেতনার দাবিদার বর্তমান সরকারের শাসনামলে ওই সব ফরমানকে সাংবিধানিক বৈধতা প্রদান করা হয়েছে।
কিন্তু শেখ মুজিব এই দক্ষিণপন্থিদের প্রধান শত্রু মনে করেননি। বামপন্থিরা তার মিত্র ছিল না এটা ঠিক, কিন্তু তারা তার জন্য তত বড় শত্রু ছিল না, যত বড় শত্রু ছিল তার আশপাশে লুকিয়ে থাকা দুর্বৃত্তরা।
যখন বাঙালিদের দাবির মুখে পাকিস্তানিরা ‘এক মানুষ এক ভোট’ নীতি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল। এর আগে ছিল সংখ্যাসাম্য; অর্থাৎ পূর্ববঙ্গের ৫৬ জনকে কেটেছেঁটে সমান করে দেওয়া হয়েছিল। পশ্চিম পাকিস্তানের ৪৪ জনের। হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দীকে দিয়েই করানো হয়েছিল ওই কাজ, নইলে পাকিস্তানিরা নিজেরা পারত না। সংখ্যাসাম্য ভেঙে পড়ল যখন, তখন জাতীয় পরিষদের ৩১৩টি আসনের মধ্যে পূর্ববঙ্গকে দিতে হলো ১৬৯টি, পশ্চিম পাকিস্তান পেল ১৪৪টি। আশা করেছিল ভোটের সময়ে বাঙালিকে বিভক্ত করা যাবে। যখন দেখল পারল না, তখন ঝাঁপিয়ে পড়ল গণহত্যায়।
জনগণ সংগ্রাম করেছে, কিন্তু মুক্তি পায়নি। রাষ্ট্র এখন কতটা স্বাধীন তা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করা যায়। কিন্তু জাতি যে মুক্ত নয় সেটা সন্দেহাতীত। জাতি বলতে জনগণকেই বোঝায়। সেই জনগণ রাষ্ট্রক্ষমতার ধারেকাছে নেই। দেশে উন্নতি হয়েছে। কিন্তু উন্নতি মানে বড়জোড় ২০ জনের উন্নতি এবং ৮০ জনের অবনতি। ধনী-দরিদ্রের তারতম্য বোঝাতে আকাশপাতালের উপমা অগ্রাহ্য নয়। ওই দুই প্রান্তের মধ্যেই বিভিন্ন স্তরের বিন্যাস। কিন্তু মুক্তির সংগ্রাম চলছে। সরবে নয় নীরবে। তাকে চলতেই হবে, নইলে আমাদের ভবিষ্যৎ কী, দাঁড়ানোর জায়গা কোথায়?
লেখক: ইমেরিটাস অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়