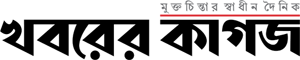এবারের বাজেটে যেসব কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য রয়েছে, অর্থাৎ প্রবৃদ্ধি, বিনিয়োগের হার, মূল্যস্ফীতি হ্রাসের মাত্রা ইত্যাদি বিষয় বাস্তবায়ন করা খুবই কঠিন হবে বলে মনে হয়। বর্তমানে দেশের বিনিয়োগ বাজার অনেকটা নাজুক অবস্থায় রয়েছে। শেয়ারবাজারে ক্রমাগত দরপতন হচ্ছে। সার্বিকভাবে ইনডেক্স অনেকটা নিচের দিকে নেমে এসেছে। সার্বিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে অর্থনীতিতে একটি সংস্কার আবশ্যক হয়ে পড়েছিল আরও আগেই এবং তা জরুরি। সে ক্ষেত্রে প্রথমেই দরকার ব্যাংক খাতে বড় ধরনের সংস্কার।
অর্থনীতির বড় এই খাতটিতে সুশাসনের যথেষ্ট অভাব আছে। ব্যাংকিং খাতে খেলাপি ঋণের কথা যদি বলা হয়, সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোনো পথনির্দেশনা দেওয়া নেই। সম্প্রতি যেসব উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, তা এই খাতকে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় আরও পিছিয়ে দিয়েছে। তা ছাড়া যেসব সংস্কার ইতোমধ্যে হয়েছে, সেগুলোর যথাযথ প্রয়োগ দেখা যায়নি। বেসরকারি বিনিয়োগও বেশ শ্লথগতিতে হয়েছে এবং হচ্ছে। কাজেই অর্থনীতিকে চাঙা রাখতে সরকারি-বেসরকারি বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। এর বিকল্প নেই।
দেশে সরবরাহ ব্যবস্থার সংকট এবং শ্রমবাজারের ওপর থাকা চাপ যদি প্রশমিত না হয়, তাহলে মূল্যস্ফীতির হারের অঙ্কটি আরও অধিকমাত্রায় বেড়ে যাবে। সে ক্ষেত্রে উৎপাদন বাড়ানোর দিকে নজর দেওয়া উচিত। মনে রাখতে হবে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি যখন দুর্বল থাকে, তখন লম্বা সময় ধরে মূল্যস্ফীতি বাড়তে দেওয়া ঝুঁকি তৈরি করে। কাজেই নীতিনির্ধারকদের মধ্যমেয়াদি রাজস্ব পরিকল্পনা করতে হবে, যেগুলোর গ্রহণযোগ্যতা থাকবে এবং দরিদ্র ও দারিদ্র্যের ঝুঁকিতে আছে এমন পরিবারকে সহায়তা অব্যাহত রাখতে হবে। এ ক্ষেত্রে আমাদের যথেষ্ট ব্যর্থতা আছে।
এই মুহূর্তে অর্থনীতির সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ মূল্যস্ফীতির পাশাপাশি বৈষম্য বেড়ে যাওয়া। মূল্যস্ফীতির কারণে নতুন করে অনেক মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে নেমে গেছে। এই সংখ্যা কত তার কোনো সঠিক পরিসংখ্যান নেই। এ ছাড়া দেশে বৈষম্য এখন বিপজ্জনক পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। এ পরিস্থিতিকে এখনই মোকাবিলা করা না গেলে তাতে নানাবিধ সমস্যা দেখা দিতে পারে। প্রবাসী আয়, খেলাপি ঋণ, রপ্তানি আয়, লেনদেনে ভারসাম্যসহ অর্থনীতির সূচকগুলোও সন্তোষজনক পর্যায়ে নেই।
নিম্ন মধ্যবিত্ত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনযাপনের মান অনেক নিচে নেমে যাচ্ছে। সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনী ভেঙে পড়লে অস্থিরতা আরও বাড়বে। দেশের বাজার নিয়ন্ত্রণ না করে বা সিন্ডিকেট না ভেঙে সরাসরি আমদানি করতে চাইলে কৃষক বা উৎপাদনকারী ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি বা বাজার ম্যানিপুলেশন করার জন্য সাধারণত কৃষক বা উৎপাদনকারী দায়ী নয়। বাজার নিয়ন্ত্রণ করে ব্যবসায়িক শ্রেণি। এরা সিন্ডিকেট করে বাজারকে অস্থিতিশীল করে থাকে। মূল্যস্ফীতি কীভাবে কমানো হবে, সে বিষয়ে কোনো দিকনির্দেশনা নেই।
আরেকটি বিষয় হচ্ছে, কালোটাকা সাদা করার যে সুযোগ দেওয়া হয়েছে তা অবশ্যই অনৈতিক। এতে করে লোকজনের মধ্যে উৎসাহের অনেকটাই ঘাটতি দেখা যাচ্ছে। এর ফলে তাদের মধ্যে একধরনের ধারণা তৈরি হয়েছে যে, সে যদি কর না দিয়ে কালোটাকা বানায় তাহলে ভবিষ্যতে এর প্রেক্ষিতে কম হারে কর দেওয়া যাবে। সুতরাং এতে করে কালোটাকার মাত্রাটা আরও বেড়ে যেতে পারে।
দেশ থেকে অনেক টাকা পাচার হয়ে যাচ্ছে, সেগুলোর আইনি প্রয়োগে যথেষ্ট অবহেলা আছে। আইনগুলো শক্তিশালী হওয়া দরকার ছিল, কিন্তু হয়নি। এসব বিষয় অর্থনীতির ভিত্তিকে আরও বেশি দুর্বল করেছে। ফলে অর্থনীতি একটা বড় রকম ঝুঁকির মধ্যে পড়ে গেছে। মুদ্রাস্ফীতি সামাল দিতে বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হলেও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা তৈরি না হয়ে আরও ঝুঁকির মধ্যে পড়েছে। যেটি মানুষের জীবনযাত্রার মানকে অনেক বেশি নিচের দিকে নামিয়ে নিয়ে এসেছে।
এমতাবস্থায় সচেতনতার সঙ্গে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে। তা না হলে অর্থনীতি আরও বেশি সমস্যাসংকুল হবে। মূল্যস্ফীতির ফলে আমাদের আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রমগুলো ব্যাহত এবং একই সঙ্গে বিনিয়োগ ব্যাহত হলে যেসব সমস্যা আছে সেগুলোর সমাধান কঠিন হয়ে যাবে। বিনিয়োগ বাড়ানোর জন্য আমাদের পরিবেশ উন্নত এবং অনুকূল করতে হবে। তাই অর্থনীতির চলমান সমস্যাগুলো সমাধান করতে হলে জোরালো ও শক্তিশালী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। পণ্যের মূল্য যাতে না বাড়ে, সে জন্য প্রয়োজনে আমদানি শুল্ক কমিয়ে দাম নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা যেতে পারে।
দেশের অর্থনীতি ঋণনির্ভর হলে চলবে না। এতে সরকারি এবং বেসরকারি খাতে অর্থনৈতিক প্রবাহ কমে যাবে। আমাদের বিনিয়োগ বাজারের অবস্থা মোটেও সন্তোষজনক নয়। বিনিয়োগ বাজার যেভাবে চলছে সেভাবে চলতে দেওয়া ঠিক নয়। আমাদের অবশ্যই চেষ্টা করা উচিত ঋণনির্ভর না হয়ে রাজস্ব আয় বৃদ্ধিতে মনোযোগ বাড়ানো।
আমাদের যে টার্গেট আছে সেটা কোনো অবস্থাতেই অর্জিত হয় না। সে ক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদের রাজস্ব আহরণ বাড়ানোর চেষ্টা করতে হবে। করের হার না বাড়িয়ে করদাতার সংখ্যা বাড়াতে হবে। যাদের কর দেওয়ার ক্ষমতা আছে তারা অনেকেই কর দেয় না। ইনকাম ট্যাক্স, অর্থাৎ যাদের টিন নম্বর আছে তারা অনেকেই রিটার্ন দেয় না।
সর্বোপরি বাজেট কতটা জনবান্ধব হলো সেটিও দেখা দরকার। হঠাৎ পণ্যের দাম বেড়ে গেলে ক্রয়ক্ষমতা কমে যায়। জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাওয়ায় মানুষের একটি অংশকে ঋণ করে জীবনযাত্রার বাড়তি খরচ মেটাতে হয়। এখন ভোক্তাঋণের সুদ বাড়ানোর ফলে তারা হয়তো চাপে পড়বেন। তবে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে ঋণের সুদহার বাড়ানোর কোনো বিকল্প নেই।
বিশ্বের বিভিন্ন দেশ সুদহার বাড়িয়ে মূল্যস্ফীতির চাপ মোকাবিলা করছে। দেরিতে হলেও আংশিকভাবে আমরা সেই পথে গেছি। তবে বিদ্যমান নীতি দিয়ে মূল্যস্ফীতি কতটা নিয়ন্ত্রণ করা যাবে, তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কাজেই সার্বিকভাবেই অস্থিতিশীল অর্থনীতির চাপ মোকাবিলায় একটি ভালো রকম সংস্কার প্রয়োজন আছে। ডলারসংকটসহ যেসব কারণে পণ্যের মূল্য বেড়ে যাচ্ছে, সেসব বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে হবে।
পণ্যের মূল্য যাতে না বাড়ে, সে জন্য প্রয়োজনে আমদানি শুল্ক কমিয়ে দাম নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা দরকার। বাজেট যেন সাধারণ মানুষের জন্য একপেশে হয়ে না যায়, সেদিকে লক্ষ রাখা জরুরি। দেশে বিদ্যমান যেসব আইন আছে, সেগুলোর যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে কঠোর আইন প্রয়োগের প্রতি বিশেষ জোর দিতে হবে। অর্থনীতির ভিত সুরক্ষায় এ বিষয়গুলোর প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজন আছে।
লেখক: সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা