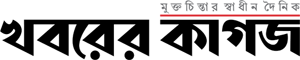পৃথিবীর মতো চাঁদ কি বসবাসের যোগ্য? চাঁদের মাটিতে কি প্রাণের সঞ্চার হতে পারে? মানুষ এমন প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে, অনেক আগে থেকে। এবার এই উত্তরের সন্ধানে চাঁদের কঠিনতম প্রান্তে মহাকাশযান পাঠিয়েছে চীন। সেখানকার মাটি খুঁড়ে পৃথিবীতে নমুনা নিয়ে ফিরেছে নভোযানটি।
চীনের চ্যাংই-সিক্স লুনার মডিউল গত মঙ্গলবার পৃথিবীতে ফিরে এসেছে। দেশটির উচ্চাকাঙ্ক্ষী মহাকাশ কর্মসূচির জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হিসেবে চাঁদের দূরবর্তী দিক থেকে প্রথমবারের মতো নমুনা সংগ্রহের ঐতিহাসিক অভিযান সফলভাবে সম্পন্ন করেছে।
চীনের রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা সিসিটিভি জানিয়েছে, পুনঃপ্রবেশ করা মডিউলটি মঙ্গলবার চীনের উত্তরাঞ্চলীয় অভ্যন্তরীণ মঙ্গোলিয়া অঞ্চলে নির্ধারিত এলাকায় সফলভাবে অবতরণ করেছে। সিসিটিভির সরাসরি সম্প্রচারে দেখা যায়, মডিউল প্যারাসুটের মাধ্যমে অবতরণ করছে এবং মিশন নিয়ন্ত্রণ কক্ষে তালি দিচ্ছে সবাই।
নিয়ন্ত্রণ কক্ষ থেকে চীনের মহাকাশ গবেষণা সংস্থার চায়না ন্যাশনাল স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (সিএনএসএ)-এর প্রধান ঝাং কেইজিয়ান বলেন, চ্যাংই-সিক্স চন্দ্র অনুসন্ধান অভিযান সম্পূর্ণ সফল হয়েছে।
সিসিটিভি জানিয়েছে, অবতরণের কয়েক মিনিটের মধ্যেই একটি অনুসন্ধান দল মডিউলটি উদ্ধার করে। সরাসরি সম্প্রচারের সময় দেখা যায়, একজন কর্মী মডিউলটির পরীক্ষা করছেন, যা একটি চীনা পতাকার পাশে ঘাসের ওপর রয়েছে।
এই সফল মিশনকে চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিন পিং ‘চিরকালের স্বপ্ন’ বলে প্রকাশ করেছেন। এ ঘটনাটি এমন সময় ঘটেছে যখন যুক্তরাষ্ট্রসহ অন্যান্য দেশও নিজেদের চাঁদে অনুসন্ধান কার্যক্রম জোরদার করছে। গত মঙ্গলবারের এক অভিনন্দন বার্তায় সি চিন পিং মিশনটিকে ‘মহাকাশ ও বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ক্ষেত্রে শক্তিশালী দেশ গড়ার জন্য আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অর্জন’ হিসেবে অভিহিত করেন।
বেইজিং ২০৩০ সালের মধ্যে মহাকাশে মহাকাশচারী পাঠানোর এবং চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে একটি গবেষণা কেন্দ্র তৈরির পরিকল্পনা করেছে। ধারণা করা হয়, চন্দ্রের দক্ষিণ মেরুতে জলীয় বরফ রেয়েছে। যেখানে যুক্তরাষ্ট্রও একটি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করতে চায়।
সিএনএসএ জানিয়েছে, চ্যাংই-সিক্স অনুসন্ধান যানটি চাঁদের দূরবর্তী দিক থেকে প্রায় দুই কেজি চাঁদের ধুলা ও পাথর নিয়ে পৃথিবীতে ফিরে এসেছে, যা চীনের গবেষকরা বিশ্লেষণ করবেন। এরপর আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানীরা এটি নিয়ে গবেষণা করবেন।
মে মাসের প্রথম সপ্তাহেই চাঁদে পাড়ি জমিয়েছিল চীন। গত ৩ মে দেশটির দক্ষিণ প্রান্তের হাইনান প্রদেশ থেকে ‘লং মার্চ-ফাইভ’ নামক রকেটে চড়ে মহাকাশে পাড়ি দিয়েছিল চ্যাং-৬।
চন্দ্রযান চ্যাংই-৬-এর লক্ষ্য ছিল চাঁদ থেকে মাটি এবং পাথর সংগ্রহ করে পৃথিবীতে নিয়ে আসা। বিজ্ঞানীদের একাংশ ভেবেছিলেন চিনের চন্দ্রযান বোধ হয় চাঁদের মাটিতে অবতরণ করতেই ব্যর্থ হবে।